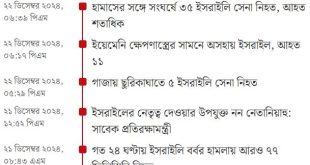এই মেলার ইতিহাস ও উৎপত্তি সম্পর্কে কয়েকটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। গুড়পুকুর মূলত সাতক্ষীরা শহরের অন্তর্গত একটি স্থান। সাতক্ষীরা এক সময় সুন্দরবনের মতোই বনবেষ্ঠিত ছিল। বন কেটে বসত করার ফলে এখন আর সেই বন নেই। এইসব এলাকার একটি নাম পাওয়া যায় ‘বুড়ন’। অর্থাৎ ওই অঞ্চল যে জলাভূমি ছিল, তার প্রমাণ এই নাম থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। ‘মনসা মঙ্গল’ -এর বেহুলা লখিন্দরের কাহিনীও এই অঞ্চলকে স্পর্শ করেছে। বেহুলা যখন সর্পদষ্ট মৃত স্বামীর লাশ কলার ভেলায় করে জলপথে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে যে ঘাটে তাঁর দেখা হয়েছিল গোদা পাটনির সঙ্গে, সেই গোদা পাটনির নামে গড়ে ওঠে ‘গোদাঘাট’ নামে একটি গ্রাম। তার এক মাইল দূরে আরেকটি জায়গার নাম হলো ‘বেহুলার ঝোড়’। সর্পসঙ্কুল সাতক্ষীরায় বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী নিয়ে প্রতি বছরই ‘মনসা পূজা’ অনুষ্ঠিত হয়। এসব এলাকায় প্রতি বছরই সর্পদংশনে অনেক মানুষের মৃত্যু হয়। এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস, সর্পদেবী মনসাকে পূজা করলে সাপের উপদ্রব থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ তারিখে গুড়পুকুরের ধারে যে বিশাল বটবৃক্ষ ছিল, তার বাঁধানো চাতালে মনসা পূজা হয়। সেই উপলক্ষে শুরু হয় মেলা। গুড়পুকুরের সেই প্রাচীন বটবৃক্ষটি এখন আর নেই। তদস্থলে একটি নতুন বটগাছ রোপণ করা হয়েছে।
জনশ্রুতি রয়েছে শহরের পলাশপোলে ঐ গুড়পুকুরের পাড়ে বট গাছের নিচে একবার এক ক্লান্ত পথিক বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। গাছের ফাঁক দিয়ে আসা রোদ পথিকের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিলো দেখে একটি বিষধর সাপ ফণা তুলে তাকে ছায়া দেয়। পথিক এই দৃশ্য দেখে মনসার উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া শুরু করেন এবং এলাকার লোকজনকে মনসা পূজা করতে বলেন। এই পূজার মিষ্টি প্রসাদ পুকুরে ফেলে দেওয়ায় পুকুরের পানি মিষ্টি হয়ে যায়। এই বিশ্বাস থেকে গোলাকৃতি পুকুরের নাম হয়ে যায় গুড়পুকুর। সেই থেকে শুরু হয় গুড়পুকুরের মেলা। এলাকার প্রবীণেরা তাদের বাল্যকাল থেকেই এ মেলা দেখে আসছেন বলে জানা যায়।
গুড়পুকুর কেন নামকরণ করা হয়েছে, এ নিয়েও একাধিক কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। পলাশপোল এলাকার প্রবীণদের কাছ থেকে আর এক রকম কিংবদন্তী শোনার কথাও বলছেন কেউ কেউ। এখানকার অত্যন্ত প্রবীণ পরিবারদের অন্যতম খান চৌধুরী পরিবার। এই পরিবারের পূর্বপুরুষেরা ব্রহ্মণ ছিলেন এবং তারা ছিলেন গৌর বর্ণের অধিকারী। গৌরবর্ণের অধিকারী খান চৌধুরীরা ওই পুকুরের মালিক ছিলেন। ‘গৌরদের পুকুর লোক মুখে ঘুরতে ঘুরতে ‘গুড়ে’ রূপান্তরিত হয়ে গুড়পুকুর হয়েছে বলে মনে করা হয়। গুড়পুকুরের মেলাটা মূলত ‘মনসা পূজা’কে কেন্দ্র করেই শুরু। কারো কারো মতে ওটা হবে ‘বিশ্বকর্মা পূজা’। পঞ্জিকা অনুযায়ী ভাদ্রের শেষ তারিখে বিশ্বকর্মা পূজা হওয়াই সঙ্গত। কেননা মনসা পূজা হয় শ্রাবণ সংক্রান্তিতে অর্থাৎ শ্রাবণের শেষ তারিখে।
কারো মতে, পুকুরটিতে পানি থাকতো না বেশিদিন; পরে স্বপ্নে দেখা গেলো পুকুরে ১০০ ভাড় গুড় ঢালতে হবে, আর সেমতে কাজ করার ফলেই পুকুরে পানি এলো, তাই এই নামকরণ। আবার শোনা যায়, পুকুরের তলদেশ থেকে একসময় মিষ্টি পানি উঠতো বলে এমন নামকরণ। কারো মতে পুকুরের পাড়ে একসময় প্রচুর খেজুর গাছ হতো। একবার সব গাছের রস সংগ্রহ করে তা দিয়ে গুড় তৈরি করে তার বিক্রীত মূল্যে খনন করা হয় এই পুকুর। আর সেই থেকেই এই পুকুরের নাম গুড়পুকুর।
মেলার এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে নানামত থাকলেও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সেই মেলার পরিধি ও ব্যাপ্তি নিয়ে সম্ভাবত কারো দ্বিমত নেই। তখন আমি স্কুলে পড়ি। বাড়ির সামনে ইটাগাছা হাট। প্রতিদিন বিকালে হাট বসতো। বাবা প্রতিদিন কোর্ট থেকে এসে ৫ পয়সা- আবার কোন কোন দিন ১০ পয়সা দিতেন। তখন ৫ পয়সায় একটা আইসক্রিম পাওয়া যেত। ঐ হাটে বিকালে সাধারণত যে আইসক্রিম পাওয়া যেত তা অনেকটা গলে যাওয়া। ফলে ৫ পয়সায় কখনো কখনো ২/৩টা আইসক্রিমও কিনতাম। মাঝে মধ্যে যে পয়সা বাঁচতো তা ফেলতাম লক্ষ্মীঘটে। এভাবেই সারা বছর পর ৪/৫ টাকা যা হতো তাই ছিলো আমার সম্বল। তা ছাড়া মেলা উপলক্ষেও বাবা চারআনা-আটআনা, মা আরো দু’এক টাকা ছাড়া আত্মীয় স্বজন যারা মেলা দেখতে আমাদের বাড়ি এসে উঠতেন তাদের কাছ থেকেও পাওয়া যেত নগদ অর্থ ছাড়াও মেলার জিনিষপত্র। তারা সঙ্গে নিয়ে যেয়ে পছন্দমত জিনিষপত্র কিনে দিতেন।
আমাদের বাড়ি তখন কেবল একতলা হয়েছে। ৫টি ঘর এবং সামনে পিছনের বারান্দা ভরে যেত আত্মীয়-স্বজনে। বোন-বোনাইরা আসতেন। সাথে তাদের ননদ-দেবরসহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন। আমাদের রাত কাটানোর জায়গা ছিলো ফাকা ছাদের উপর। যদিও মূল মেলার সময় আমরা রাত কাটাতাম সারারাত সিনেমা দেখে। বাড়িতে কখনো কখনো দাদী নানীরাও আসতেন। তাদের কাজ ছিলো রান্না ঘর সামলানো। প্রায় সারাটা দিনই তাদের কাটতো রান্না ঘরে।
সাধারণত মূল মেলার তিনদিন শহরের প্রায় সকল স্কুল ছুটি থাকতো। আমরা সকাল হলেই বেরিয়ে পড়তাম মেলা দেখতে। হাওয়াই মিঠাই খেয়ে মুখ লাল করে ঘুরে বেড়াতাম। কখনো রসমন্ডা, বাতাসা, গজাসহ মিস্টি-মিঠাই কিনে বাড়ি ফিরতাম। আখ কিনে চিবুতে চিবুতেও ঘুরতাম বিভিন্নস্থানে। নাগরদোলায় চড়ার আনন্দটাই ছিল আলাদা। তারপর দু’আনা চারআনা দিয়ে প্রথম দিকে মাটির নৌকা, গাড়ি, মাথা কাপানো বুড়ো দাদাসহ বিভিন্ন পুতুল কিনে নৌকায় দড়ি বেঁধে পাকারাস্তা ধরে টানতে টানতে বাড়ি আসতাম। তারমধ্যে নৌকা বা গাড়ির চাকা শেষ। বুড় দাদার দাড়ি খুলে গেছে। তাই আরো পরের দিকে মাটির খেলনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে টিনের প্রতি আকর্ষণ শুরু হয়। পিস্তল কিনে কাগজে লাগানো বারুদের ব্যান্ডিল নিয়ে শুরু করতাম চোর-পুলিশ আর দারোগার খেলা। দু’একদিনের মধ্যে ভেঙে যেয়ে পিস্তলও শেষ। তাই আরো বেশী দামের ভালো পিস্তল কিনতাম মেলার শেষের দিকে। তখন শুনতাম মেলার শেষের দিকে দাম কমে যায়। তাই প্রতিদিন যেয়ে দাম শুনতাম, দাম কমেছে কি না? লঞ্চ কিনতাম। আর তার পলতেতে আগুন ধনিয়ে পানিতে ছেড়ে দিতাম। বড়-বড় করে চলতো কিছু সময়। তারপর পানি ঢুকে লঞ্চ শেষ।
গুড়পুকুরের মেলা ছিলো সাতক্ষীরাবাসির মিলনমেলা। হিন্দু মুসলিম সব সম্প্রদায়ের মানুষের এক হওয়ার মহা উৎসব। যে উৎসবের ঢেউ ছড়িয়ে পড়তো তৎকালীন সাতক্ষীরা মহাকুমার সকল এলাকায়। খুলনা যশোরসহ দুর দুরন্ত থেকে আসা মানুষের মধ্যে।
আমার বাবা সারা বছর ধরে এই মেলার জন্য অপেক্ষা করতেন ঘরের একটি দরজা অথবা জানালা বা চেয়ার-টেবিল কেনার জন্য। মা অপেক্ষা করতেন খোন্তা কড়াই দা বটি ধামা কুলা ঝুড়ি বা অন্য কোন জিনিষ কেনার জন্য। শহরের বাইরের মানুষেরও অপেক্ষা ছিলো এ মেলার জন্য। কৃষক তার চাষের জিনিষপত্র তথা লাঙ্গল ফলা ইত্যাদী কেনার জন্য অপেক্ষা করতেন। শ্রমিক তার নির্মাণ কাজের জন্য হাতুড়ি কড়াইসহ প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতেন এই মেলা থেকে।
এতো গেল ক্রেতাদের কথা। কাঠ মিস্ত্রিরা সারা বছর ধরে তার কাজের ফাকে কাঠের জিনিষপত্র বানিয়ে নিজ বাড়ি ভরতেন। কুমাররা মাটির জিনিষপত্র বানিয়ে মজুদ করতেন। নার্সারী ব্যবসায়ীরা সারা বছর ধরে চারা তৈরী করতেন। কামাররা বানাতেন লৌহজাত জিনিষপত্র। বিভিন্ন পেশার মানুষ সারা বছর ধরে গায়ে গতরে খেটে এসব তৈরী করতেন মেলায় বিক্রি করে একসাথে অনেক টাকা উপার্জনের জন্য। মেলার প্রথমে দাম একটু বেশ হলেও পরে কম দামেই সব বিক্রি করে একসাথে অনেকগুলো নগদ টাকা নিয়ে তারা বাড়ি ফিরতেন। তাদের লোকসান হতো না। কারণ অবসর সময়েই কমদামে সংগ্রহ করা সামগ্রী দিয়েই এগুলো বানাতেন তারা।
শুনেছি সাতক্ষীরার প্রাণসায়রে লঞ্চ চলতো। তবে আমি তা দেখেনি। আমি দেখেছি সাতক্ষীরা বড়বাজারের কাছে প্রাণসায়র খালে একটা বড় দোতলা লঞ্চ বাধা ছিল বেশ কয়েক বছর। বর্তমান সাতক্ষীরা নাইট স্কুলটি তখন ছিল সাতক্ষীরার এসডিপিও’র অফিস। সামনে লেখা ছিল জ্ঞান মন্দির। তার সামনে থাকতো স্পীডবোট বাধা। পানি উন্নয়ন বোটের স্পীড বোট থাকতো বড়বাজারের দক্ষিণ পাশে খাদ্যগুদামের দক্ষিণ দিকে। আর স্টেডিয়ামের সামনে বর্তমান টেনিস গ্রাউন্ড ছিল তখন বিডিআর ক্যাম্প। ক্যাম্পের পাশে বাধা থাকতো বিডিআর ও এসডিও’র স্পিডবোট। প্রাণসায়রের পানি উন্নয়ন বোট এলাকা থেকে গার্লস স্কুলের কাঠের পুল পর্যন্ত থাকতো ছোট বড় শতশত গহনা ও টাবরু নৌকা। মেলার বিভিন্ন সামগ্রী আসতো ঐ সব নৌকায়। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ নৌকায় করে মেলায় এসে রাত কাটাতো সেখানে। রান্না-বান্না খাওয়া দাওয়া চলতো ঐসব নৌকায়।
শহরের সঙ্গীতা সিনেমা হলের (হলটি নির্মিত হয় সত্তরের দশকের শেষের দিকে) উত্তর পাশের রাস্তার দু’ধারে সারিবদ্ধভাবে বসতো অসংখ্য নার্সারীর দোকান এবং তা বর্তমান নিউমার্কেট পর্যন্ত যেত। তার উত্তর পাশে প্রায় বর্তমান জজকোর্ট পর্যন্ত বসতো কাঠের ফার্নিচার, দা-বটি-খোন্তা-কোদাল-লাঙ্গলসহ বিভিন্ন লৌহজাত সামগ্রী। পলাশপোল স্কুলে বসতো বাশ বেতের বিভিন্ন সামগ্রীর দোকান। আর সেই সাথে নাগোরদোলা। পাশে গুড়পুকুর কান্দায় বসতো জিলাপি বাতাশাসহ হরেক রকমের মিষ্টি মিঠাইয়ের দোকান। পলাশপোল বর্তমান সেটেলমেন্ট অফিসের এলাকাটি (আমতলা নামে খ্যাত) ছিল সার্কাসের এলাকা। এখানে সার্কাস বসতো। তখন সাতক্ষীরা নিউমার্কেট নির্মিত হয়নি। ঐ স্থানে টিনের বেড়া দিয়ে উপরে চট টাঙিয়ে প্রোজেক্টর মেশিনের মাধ্যমে অস্থায়ী সিনেমা হল বসানো হতো। এছাড়াও পুতুল নাচও দেখানো হতো এখানে।
লাবনী সিনেমা হলের সামনের রাস্তাটির দু’ধারে পাকাপুল পর্যন্ত বসতো হরেক রকমের খেলনা সামগ্রীসহ মনোহরি পন্যের দোকান। পাকাপুলের বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা সড়কে থাকতো কমদামী কাঠের চেয়ার টেবিল চৌকি দরজা জানালাসহ কাঠজাত সামগ্রীর দোকান। পাকাপুলের উত্তর পাশের পাওয়ার হাউজের পাচিলের পূর্ব পাশে বসতো আখ লেবুসহ বিভিন্ন ফলের দোকান। মাটির খেলনার দোকান বসতো এর আশে পাশের এলাকায়। ইলিশের দোকান বসতো ইটাগাছা হাটের সামনে। আর সাতক্ষীরা স্টেডিয়ামে কখনো কখনো বসতো যাত্রা-সার্কাস-পুতুলনাচের আসর। এছাড়া ইটাগাছা হাটের সামনেও আখ লেবুর দোকান বনতো।এ রকমই ছিল সাতক্ষীরার গুড়পুকুরের মেলার পরিধি। এক এক বছর এর কম বেশী হতো।
ভাদ্র মাসের ৩১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলা শুরু হওয়ার ১৫ দিন পূর্ব থেকে শুরু হতো দোকান পাট বানানোর কাজ। মূল মেলা ৩দিনের হলেও তা চলতো মাসব্যাপি। তারপর পুলিশ ভেঙে না দেওয়া পর্যন্ত ব্যবসায়ীরা থেকে যেত। মূল মেলার তিনদিন সাতক্ষীরা-কালিগঞ্জ সড়ক ছাড়া মেলা এলাকায় তেমন কোন যানবাহন চলতো না। চলার কথাও নয়। পাকাপুল থেকে লাবনী পর্যন্ত মানুষের ভীড় ঠেলে যাতায়াত করতে কখনো কখনো আধাঘন্টাও সময় লেগে যেত। দিনরাত ২৪ ঘন্টার শেষ রাতের কিছু সময় ছাড়া প্রায় সকল সময় মেলার দোকান-পাট খোলা থাকতো।
মেলায় দেশের বিভিন্নস্থান থেকে আগত হাজার হাজার মানুষের মধ্যে যাদের শহরে আত্মীয়স্বজন ছিল তারা তাদের বাড়িতে উঠতেন। দক্ষিণের মানুষের থাকা খাওয়া ছিল নৌকার মধ্যে। এছাড়াও আরো বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য তখনকার একমাত্র সিনেমা হল লাবনী, পরে সঙ্গীতা, নিউমার্কেটের অস্থায়ী সিনেমা হলে সারা রাত ব্যাপি এক টিকিটে ২/৩টি ছবি দেখার ব্যবস্থা করা হতো। এছাড়া যাত্রা চলতো সারারাত। ফলে বিপুল সংখ্যক মানুষের রাত কাটানোর ব্যবস্থা হয়ে যেত এভাবেই। এরপরও পার্কে, পুরাতন বাসস্টান্ডে এবং বিভিন্ন বাসা বাড়ির সামনের বারান্দায়ও মানুষ রাত কাটাতো।
সাতক্ষীরার ঐতিহ্যের এই মেলা আশির দশকের শুরুর দিক থেকেই তার জৌলুস হারাতে থাকে রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের চাঁদাবাজির কারণে। তারপরও শুরুটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় হলেও শেষটা হতো ভালোভাবেই। তবে শহরে একের পর এক বাড়ি ঘর দোকান পাট মার্কেট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কারণে মেলার স্থান অনেকটা সংকীর্ণ হতে শুরু করলেও মানুষের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা কমেনি। মেলার ধারাবাহিকতা ছিল ঠিকই। কিন্তু ২০০২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মেলা উপলক্ষে সাতক্ষীরা স্টেডিয়ামে বসা সার্কাস প্যান্ডেল এবং শহরের রকসি সিনেমা হলে জঙ্গি বোমা হামলায় ৩ জন নিহত এবং অর্ধ শতাধিক আহতের ঘটনার পর এই মেলা তার জৌলুস হারায়। কয়েক বছর বন্ধ থাকে। এরই মধ্যে অল্প সময়ে চিরচেনা সেই সাতক্ষীরা শহরের চেহারা সম্পূর্ণভাবে পাল্টে যায়। পূর্বে সেই মেলার স্থানগুলো এখন বাড়ি ঘর দোকান পাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে নতুন করে গত কয়েক বছর মেলা বসে শহীদ আব্দুর রাজ্জাক পার্কে সীমিত পরিসরে। কিছু অংশ পলাশপোল স্কুলে। এ মেলা এখন আর জেলাবাসীকে আগের মত আকর্ষণ করে না। আত্মীয় স্বজন মেলার কথা ভুলে গেছে। দূর-দূরান্ত থেকে সেই মানুষ আর আসে না। সারা বছর ধরে কেউ আর মেলার জন্য জিনিষপত্র বানায় না।
প্রাণসায়র আজ প্রায় অস্তিত্বহীন। জোয়ার-ভাটা আর হয় না। গহণার বা টাবরুর নৌকা আর চলে না। দক্ষিণের মানুষেরা এখন আর নৌকায় শহরে এসে খাওয়া দাওয়া সেখানে সারে না। শহরের বাড়িতে বাড়িতে সেই মিলন মেলা এখন আর বসে না।
তারপরও মেলার সেই স্মৃতি বাঁচিয়ে রেখে পুরাতন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মেলা বসছে এখনো। এ মেলা আমাদের ঐতিহ্যের। এ মেলা অসাম্প্রদায়িক বাঙালি চেতনার এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এ মেলা আমাদের সব সম্প্রদায়ের মানুষের মিলন মেলা।লেখক: উপদেষ্টা সম্পাদক, দৈনিক পত্রদূত ও সাবেক সভাপতি, সাতক্ষীরা প্রেসক্লাব।
 ক্রাইমবার্তা নির্যাতিত মানুষের পাশে
ক্রাইমবার্তা নির্যাতিত মানুষের পাশে